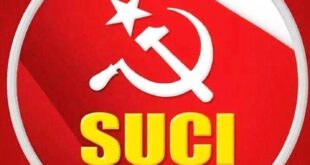একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিরোধিতা এবং অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের মারাত্মক ভয় ভারতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী অংশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (রিফরমিস্ট অপজিশনাল) ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইহার ভূমিকা ছিল সমান আপসমুখী। ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্র উভয়ের সঙ্গে আপস রফা করিয়াই গড়িয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করার ফলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা সমাজের গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পূর্ণ করা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একীকরণের কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না এবং হয়ও নাই। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনাকালে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে একটি জাতিতে পরিণত হইল বটে, কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য এবং ধর্মীয় বন্ধনের বিরুদ্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করার দরুন ভারতীয় জনসাধারণ ধর্ম-বর্ণ-ভাষাগত কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসাবেই টিঁকিয়া রহিল।
… … …
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার পথে সমাজ গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ধর্মকে পুরোপুরি শক্তিহীন করিয়াই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যথার্থ সংহত করিয়া জাতি গঠন সম্ভবপর। না জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব, না জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব গঠনের কথা যাঁহারা বলিতেন তাঁহারা– কেহই ভারতীয় জাতিগঠনের এই সমস্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজগুলি সমাধা করেন নাই। সুতরাং সমস্ত সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করিয়া একটি জাতিগঠন সম্ভব হয় নাই। নেতাদের পক্ষে আন্তরিকতার অভাবের জন্য ইহা হয় নাই তাহা নহে, আমার বক্তব্য হইতেছে, দৃষ্টিভঙ্গির অপরিচ্ছন্নতা ও ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিশেষত মুসলিম জনসাধারণকে আন্দোলনের সাথে সামিল করিয়া একটি জাতিগঠনের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। আমি ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই অতীতের ঘটনাবলী এখানে উল্লেখ করিতেছি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি সফল করিবার জন্য যে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠা উচিত ছিল, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা গ্রহণ করার ফলেই তাহা তাহাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা, অপরদিকে বহিঃক্ষেত্রে ভারতীয় জনসাধারণকে একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনের সম্মুখীন হইয়া ইহা হিন্দুধর্মের উদারতা ও সহনশীলতার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে সংহত করিয়া একটি জাতি গঠনে ব্রতী হইয়াছিল। এমনকি জাতীয় নেতৃত্ব ক্ষমতালাভের পূর্বে এই বিষয়ে যে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল, ক্ষমতালাভের পরেও তাঁহারা তাহার সংশোধন করেন নাই। বরং আমাদের দেশের বর্তমান শাসকবৃন্দ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপূরিত কর্মসূচি সম্পূর্ণ করার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং কুসংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। ফলে সমাজবিরোধী শক্তি ও মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে কার্যকরী ভাবে সাহায্য করিতেছেন। এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আমরা দেখিতে পাই পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা প্রাক-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বাস্তবে সমস্ত ধর্মের বিকাশে সমান উৎসাহ প্রদান এবং সমস্ত ধর্মাবলম্বী লোকদের ধর্মপ্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানে রাষ্ট্র কর্তৃক সমান সুযোগ প্রদানের নীতিতে পর্যবসিত করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, এই ধরনের পরিবেশেই হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের দাবি বাস্তবে দৃঢ় ভিত্তি পাইতেছে। ইহা বোঝা উচিত যে, যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে কোনও ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার পালন এবং ধর্মীয় প্রচারকে উৎসাহ প্রদান করা বোঝায় না। অথবা ইহার দ্বারা জনসাধারণের উপর ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও বোঝায় না। এবং এই ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা কোনও একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা কোনও মতেই বোঝায় না। একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মকে নাগরিকদের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। সুতরাং উহা ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধর্মীয় প্রচারকে যেমন কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করে না, তেমনি প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে না। বিপরীতপক্ষে ইহা ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণ এবং কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করে না এ রূপ জনসাধারণ– উভয়েরই সমান অধিকারের নীতিকে কার্যত স্বীকার করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে সফল করার মধ্য দিয়া ইহা সমাজের গণতন্ত্রীকরণ সাধন করে এবং ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও রাষ্ট্রের উপর হইতে ধর্মের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে। আমাদের দেশের বর্তমান বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট মনোভাবের ফলে আজও ভারতীয় জনসাধারণ ভাষা, ধর্ম, বর্ণ এবং উপজাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের সমষ্টি মাত্র। যখন পাশ্চাত্যের আধুনিক জাতিগুলি যাহারা সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক বিভেদমূলক আচার, রীতিনীতি এবং রাষ্ট্র ও সামাজিক আচার রীতিনীতির উপর চার্চের প্রভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সফল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটাইয়া জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারাও ধর্মীয় উন্মাদনা, বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত দাঙ্গা (আমেরিকায় নিগ্রোদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও গ্রেট ব্রিটেনে বর্ণভিত্তিক দাঙ্গা উল্লেখযোগ্য) প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই, তখন ইহা সহজেই অনুমেয় যে যখন ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণহিন্দু, তফসিল জাতি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ও খ্রিস্টান এবং অসমীয়া, বাঙালী, ওড়িয়া, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত দিক দিয়া বিভক্ত, তখন এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ কত গভীরে নিহিত। সুতরাং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটানোই আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। (সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কেঃ নির্বাচিত রচনাবলি, ২য় খণ্ড)